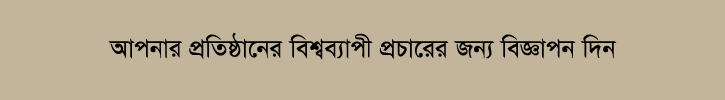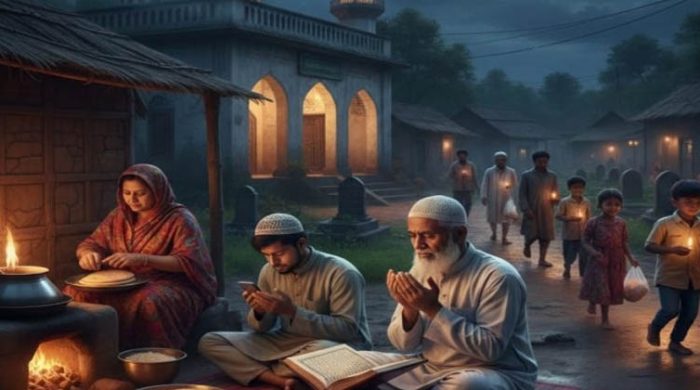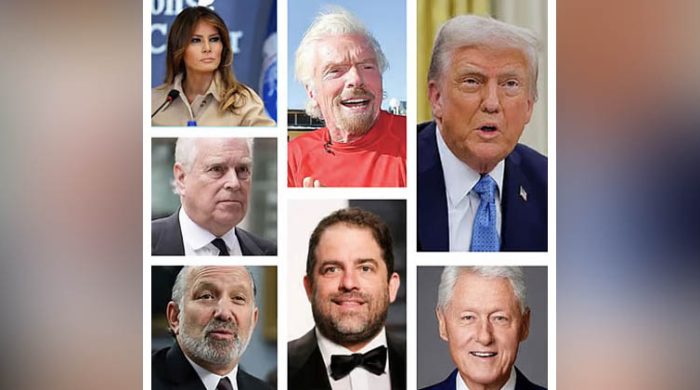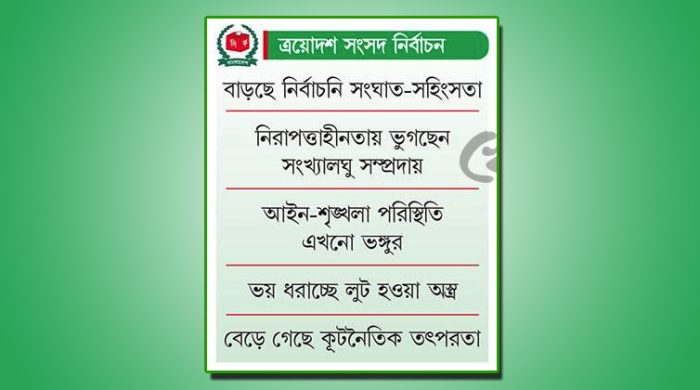টেকসই ও সাশ্রয়ী মহাসড়ক নির্মাণে বিটুমিনের বদলে কংক্রিটে ঝুঁকছে সরকার
- আপডেট সময়: শুক্রবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫
- ২০৬ দেখেছেন :

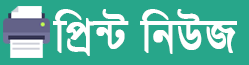
নিজস্ব প্রতিবেদক
বাংলাদেশে মহাসড়ক নির্মাণে বিটুমিনের বদলে কংক্রিট ব্যবহারের দিকে ঝুঁকছে সরকার। সাম্প্রতিক পরীক্ষায় দেখা গেছে, রিজিড পেভমেন্ট বা কংক্রিট সড়ক বেশি টেকসই, রক্ষণাবেক্ষণে কম খরচ হয় এবং দেশের জলবায়ুর প্রভাব ও যানবাহনের চাপ সামলাতে সক্ষম।
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের (সওজ) তথ্য অনুযায়ী, বিটুমিন ও পলিমার মডিফায়েড বিটুমিন (পিবিএম) দিয়ে তৈরি সড়কজের প্রাথমিক নির্মাণ খরচ কম হলেও—এর আয়ুষ্কাল স্বল্প। এ ধরনের সড়কের ২০ বছরের মধ্যে অন্তত চারবার বড় ধরনের সংস্কারের প্রয়োজন হয়, পাশাপাশি নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের খরচ তো আছেই, যা সামগ্রিক খরচ অনেক বাড়িয়ে তোলে। উচ্চ তাপমাত্রা, শীত, জলাবদ্ধতা আর অতিরিক্ত বোঝাই ট্রাকের ভারে দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত হয় এসব সড়ক।
এই অংশের কাজ করছে চীনা প্রতিষ্ঠান সিনোহাইড্রো ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যুরো-৮ কোম্পানি লিমিটেড। কংক্রিট ব্যবহারের ফলে হালকা বৃষ্টিতেও কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়, যা প্রকল্পের সময়সীমা কমাতে সাহায্য করে। তবে রাস্তা চালু করার আগে ২৮ দিনের ‘কিউরিং’ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়।
সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সিলেট অঞ্চলের অতিবৃষ্টি, জলাবদ্ধতা এবং ঘন ঘন পাথরবোঝাই ওভারলোড ট্রাক চলাচল বিটুমিন দিয়ে নির্মিত সড়ককে ব্যয়বহুল এবং অটেকসই করে ফেলছে।
কংক্রিট সড়কের সুবিধা:
সওজের বিস্তৃত তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনায় দেখা গেছে, কংক্রিট সড়ক বিটুমিন সড়কের তুলনায় দীর্ঘস্থায়ী ও অধিক সহনশীল। এন-১ (ঢাকা-চট্টগ্রাম), এন-৩ (ঢাকা-ময়মনসিংহ) এবং এন-৫ (ঢাকা-রংপুর) মহাসড়কের বিভিন্ন অংশে কংক্রিট দিয়ে নির্মিত অংশগুলো বছরের পর বছর ধরে কার্যত কোনো রকম রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন পড়েনি, যদিও সেখানে অতিরিক্ত বোঝাই যানবাহন চলাচল ও দুর্বল ড্রেনেজ ব্যবস্থার মতো প্রতিকূল পরিস্থিতি বিদ্যমান।
সে তুলনায়, বিটুমিন সড়ক— এমনকি পলিমার-মডিফায়েড সংস্করণও— বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ সংস্কারের প্রয়োজন পড়েছে। বিশেষ করে টোল প্লাজা ও বাজার এলাকার মতো চাপযুক্ত স্থানে কংক্রিট সড়ক অত্যন্ত সফল প্রমাণিত হয়েছে, এসব অংশে জলাবদ্ধতা প্রচলিত বিটুমিনে তৈরি সড়কের দ্রুত ক্ষতি করে।
কংক্রিট মহাসড়ক নির্মাণের বৈশ্বিক ধারা: যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের অভিজ্ঞতা:
বিশেষজ্ঞরা জানান, যুক্তরাষ্ট্রে সড়ক নির্মাণে কংক্রিটের ট্রায়াল শুরু হয় ১৯৭৩ সাল থেকে। তখন আমেরিকায় পেট্রোলিয়াম পণ্য রফতানির ওপরে নিষেধাজ্ঞা দেয় আরব দেশগুলো। এদিকে পেট্রোলিয়াম না আসায়, এর উপজাত হিসাবে পাওয়া বিটুমিনেরও দুষ্প্রাপ্যতা তৈরি হলো। ফলে প্রাথমিক খরচ বেশি হলেও পরবর্তীতে তারা কংক্রিটের পেভমেন্ট বানানো আরম্ভ করল। যত হাইওয়ে আছে তখন একটু খরচ বেশি হলেও— তারা বিটুবিনের রাস্তা থেকে সরে গেলে কংক্রিটে।
শুরুর দিকে দ্রুত টায়ার ক্ষয় ও অতিরিক্ত ধূলাবালুর মতো সমস্যার মুখে পড়লেও—ফেডারেল ও অঙ্গরাজ্য পর্যায়ের বিস্তৃত গবেষণার মাধ্যমে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা হয় এবং সড়কের মানোন্নয়ন সম্ভব হয়।
গবেষণায় আরও দেখা যায়, কংক্রিট সড়কে ট্রাক প্রায় ২০ শতাংশ কম জ্বালানি খরচ করে, কারণ শক্ত কংক্রিট সড়ক ভারী চাকার নিচে দাবে না, যেখানে নমনীয় বিটুমিন সড়ক চাপে কয়েক মিলিমিটার বসে যায়।
সময় গড়ানোর সঙ্গে ট্রাক মালিকরাও কংক্রিট সড়কের দাবি জানাতে শুরু করে, ফলে যুক্তরাষ্ট্রে এর ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয় এবং পরে জার্মানি ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও এই প্রবণতা ছড়িয়ে পড়ে।
একইভাবে, গবেষণা-নির্ভর অভিজ্ঞতার আলোকে ভারত ২০১৭ সালে ঘোষণা দেয় যে, নতুন কোনো জাতীয় মহাসড়ক আর বিটুমিন দিয়ে নির্মিত হবে না।
বাংলাদেশের মতোই গ্রীষ্মমন্ডলীয় দেশ ভারতে প্রচুর বৃষ্টিপাত, ঘন ঘন জলাবদ্ধতা ও দুর্বল ড্রেনেজ ব্যবস্থার কারণে বিটুমিন সড়ক টেকসই হয়নি এবং দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গবেষণায় প্রমাণিত হয়, কংক্রিট সড়ক অধিক টেকসই ও ব্যয় সাশ্রয়ী।
ফলে ভারত সরকার দৈনিক ৩০ কিলোমিটার (বা বছরে প্রায় ১১,০০০ কিলোমিটার) মহাসড়ক নির্মাণ ও সংস্কারের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে, যেখানে নতুন সব সড়ক কংক্রিট দিয়েই তৈরি করা হচ্ছে, বিটুমিন নয়।
বুয়েটে প্রথম কংক্রিট সড়ক:
১৯৯৬ সালে বুয়েট ক্যাম্পাসে প্রায় ৯০ শতাংশ রাস্তা কংক্রিটে নির্মিত হয়। এর আগে ক্যাম্পাসের রাস্তাগুলো নিয়মিত মেরামত করতে হতো, বিটুমিন ড্রাম গরম করতে তুষ পোড়ানোর কারণে পরিবেশ দূষণ হতো। কংক্রিটে পরিবর্তনের পর থেকে সড়কগুলোতে আর মেরামতের প্রয়োজন হয়নি।
অধ্যাপক শামসুল হক বলেন, “কংক্রিটের রাস্তা অতিরিক্ত লোডিং, জলবদ্ধতা ও উচ্চ তাপমাত্রার মতো সমস্যাগুলো মোকাবিলায় বিটুমিনের চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর। বাংলাদেশ সরকার সাশ্রয়ী মূল্যে টেকসই উন্নয়নের স্লোগান বাস্তবায়নে কংক্রিট পেভমেন্টকে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করতে পারে।”